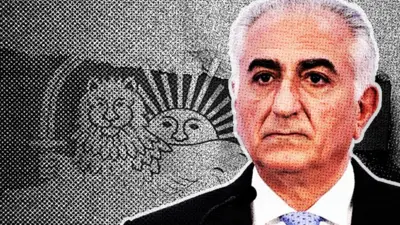বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে যে ছয়টি আইন বেশি বিতর্কিত হয়েছে

ছবির উৎস, Getty Images
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে গত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময়ে এমন কিছু আইন এসেছে যেগুলো নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা সময়ে সমালোচনা ও বিতর্ক হয়েছে।
এসব আইন মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী বলে মানবাধিকার কর্মীরা সমালোচনা করেছেন। এরমধ্যে কয়েকটি আইন বাতিল হলেও অনেকগুলো আবার নানা সমালোচনা সত্ত্বেও বহাল রয়েছে।
কী ছিল এসব আইন তা এক নজরে দেখে নেয়া যাক-
বিশেষ ক্ষমতা আইন
বিশেষ ক্ষমতা আইনটি পাস করা হয়েছিলো ১৯৭৪ সালে। এই আইন অনুযায়ী, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য যে কাউকে আটক করতে পারতো।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এই আইনটি পাস করা হয়।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যুদ্ধের পর পরই ওই সময়টাতে অনেকের হাতে অস্ত্র ছিল, পুলিশ বাহিনী সুসংগঠিত ছিল না, বামপন্থীরা রাতারাতি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতে শৃঙ্খলা ফেরাতেই এই আইনটি করা হয়েছিল।"
আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ ১৯৭৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি আইনটি পাস করে। আইন পাশের পর আওয়ামী লীগ ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। সমালোচকরা এই আইনটিকে 'কালো আইন' বলেও অভিহিত করে।
যেসব কারণে আইনটির সমালোচনা করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আইনটির অধীনে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন যে কোন ব্যক্তিকে আটক করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল পুলিশকে।

ছবির উৎস, Getty Images
"এখানে ভয়ংকর দিকটি হচ্ছে, আটক করার জন্য অপরাধ করার দরকার নেই, বরং সরকার যদি মনে করে বা সন্দেহ করে যে কেউ অপরাধ করতে পারে, তাহলেই এই আইনে তাকে আটক করা যাবে," বলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি শাহদীন মালিক।
মি. মালিক বলেন, আটকের পর আদালতে হাজির না করেই সরাসরি জেলে পাঠানোর এখতিয়ার এই আইনে দেয়া ছিল। সাধারণত জেলে পাঠানোর আদেশ আদালত থেকে দেয়ার নিয়ম থাকলেও এই আইনে সরকার ছয় মাসের জন্য জেলে পাঠানোর আদেশ দিতে পারে এবং ছয় মাস করে বাড়িয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাউকে আটক রাখতে পারে।
বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় গেলে বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন সময়ে দিয়েছে। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর আর সেটি বাতিল করেনি।
১৯৯০ সালে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে এই আইনের ১৬(২)ধারা বাতিল করা হয়। যেখানে বলা হয়েছিল, কোনো ব্যক্তি ক্ষতিকর কোনো কাজ করলে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।
মুজিব হত্যা ও ইনডেমনিটি আইন
বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি এড়ানোর সুযোগ করে দিতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বা দায়মুক্তি আইন জারি করা হয়েছিল।
শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতাসীন হওয়া তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ এই দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করেন।

সেসময় বাংলাদেশে সংসদ অধিবেশন না থাকার কারণে আইন পাস করা সম্ভব ছিল না বলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ আকারে এটি জারি করেন।
পরে ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সংসদে এই অধ্যাদেশটি উত্থাপন করে অনুমোদন দেয়া হয়। ফলে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে আইন হিসেবে পাস হয়। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এর বৈধতা দেয়া হয়েছিল।
অর্থাৎ শেখ মুজিব হত্যাকারীদের যাতে বিচার না করা যায় সেজন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে বৈধতা দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমানের আমলে গঠিত সংসদ।
আইনজীবি শাহদীন মালিক বলেন, “আইনে বলা হলো ১৫ই অগাস্ট যে ঘটনা ঘটেছে বা মৃত্যু হয়েছে বা ক্ষতি হয়েছে তার জন্য কারো বিচার হবে না।”
১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর সংসদে বিলের মাধ্যমে ইনডেমনিটি আইন বাতিল করা হয়। এর ফলে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।
জননিরাপত্তা আইন
দুই হাজার সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ত্বাধীন সরকার ‘জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন আইন ২০০০’ পাস করে। এই আইনে অভিযুক্তকে জামিন দেয়া যাবেনা সহ আরো কয়েকটি কঠোর বিধান ছিল। যার কারণে এটি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।
এই আইনটিকে কেন্দ্রে করে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সাহাবউদ্দিন আহমদ সাথে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের তিক্ততা তৈরি হয়েছিল। বিতর্কিত জননিরাপত্তা আইনে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান রাষ্ট্রপতি সাহাবউদ্দিন আহমদ।
ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দরপত্র ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ, গাড়ি ভাঙচুর ও সম্পদের ক্ষতিসাধন, যান চলাচলে বাধা, মুক্তিপণ দাবি ও আদায়, ভয়ভীতি সৃষ্টি সংক্রান্ত নানা অপরাধকে এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।
বিএনপি সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০০২ সালে জননিরাপত্তা আইন বাতিল করা হয়। এর পরিবর্তে বিএনপি সরকার ‘আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ’ নামে নতুন একটি আইন পাস করে।
তবে এটি আসলে জননিরাপত্তা আইনের মতোই বলে সমালোচনা রয়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সব সময়েই এটিকে বিরোধীদল নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করেছে বলেও সমালোচনা রয়েছে।

ছবির উৎস, সংবাদপত্র থেকে নেয়া।
অপারেশন ক্লিন হার্ট এবং দায়মুক্তি
বিবিসি বাংলার সর্বশেষ খবর ও বিশ্লেষণ এখন সরাসরি আপনার ফোনে।
ফলো করুন, নোটিফিকেশন অন রাখুন
বিবিসি বাংলার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিবিসি বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট। কিন্তু সেটি পূরণ করতে পারেনি তারা। উল্টো সেসময় ঢাকার রাস্তায় একের পর এক ওয়ার্ড কমিশনরাকে গুলি করে হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটেছিল।
এই প্রেক্ষাপটে ২০০২ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে সারাদেশে একযোগে অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনী। নির্বিচারে তল্লাসি ও গ্রেফতার চালানো হয়। এই অভিযানের নাম দেয়া হয়েছিল অপারেশন ক্লিন হার্ট।
অপারেশন ক্লিন হার্ট এর আওতায় সেনাবাহিনী বিভিন্ন জায়গায় যাদের আটক করে তাদের মধ্যে অন্তত ৪০ জনের বেশি হেফাজতে মৃত্যু হয় বলে সংবাদ মাধ্যমের খবরে প্রকাশিত হয়। সেনাবাহিনী মোট ৮৪ দিন অভিযান পরিচালনার পর তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। যেদিন থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার শুরু হয়, তাদের আগের দিন “যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ ২০০৩” জারি করা হয়। এর মাধ্যমে শেষ হয় অপারেশন ক্লিনহার্ট।
শাহদীন মালিক বলেন, “যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইন ২০০৩- এই আইনের অধীনে বলা হলো যে, অক্টোবর ২০০২ থেকে জানুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত যৌথ বাহিনীর অভিযানে কারো মৃত্যু হলে, আহত হলে, সম্পত্তি ক্ষুণ্ণ হলে, এইটার জন্য কোন আদালতে কোন মামলা করা যাবে না। ”
মানবাধিকার কর্মীরা তখন বলেছিলেন যে, হেফাজতে যেসব মৃত্যু হয়েছে এই আইনের মাধ্যমে তাদের পরিবারের বিচার চাওয়ার পথও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।
অপারেশন ক্লিনহার্টের জন্য দায়মুক্তি আইনকে চ্যালেঞ্জ করে ২০১২ সালে জেড আই পান্না নামে একজন মানবাধিকার আইনজীবী হাইকোর্টে রিট মামলা করেন। তার যুক্তি ছিল এ ধরনের দায়মুক্তি আইন বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী। সেই রিট মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই হাইকোর্ট ঐ দায়মুক্তি আইনকে অবৈধ ঘোষণা করে।

ছবির উৎস, Getty Images
সন্ত্রাস বিরোধী আইন
আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে ২০০৪ সাল থেকে সন্ত্রাস বিরোধী আইন করার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে সন্ত্রাসবিরোধী আইন গৃহীত হয়।
তবে এটি আইন হিসেবে সংসদে পাস হওয়ার আগে ২০০৮ সালের জুন মাসে সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্বাবধায়ক সরকার সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ জারি করে।
এই অধ্যাদেশটি ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিল আকারে উত্থাপন করে সেটি আইন হিসেবে পাস করা হয়।
তখন 'অধিকার' নামে একটি মানবাধিকার সংস্থা অভিযোগ করে, আইনটিতে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের’ যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এই আইনের অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
আইনটি কার্যকর হওয়ার দুই বছর পর সংস্থাটি অভিযোগ করে, এই আইনটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।
পরে এই আইনটি ২০১২ এবং ২০১৩ সালে সংশোধন করা হয়। এরমধ্যে ২০১৩ সালের সংশোধনীতে বিদেশে কোনও অপরাধ করে দেশে ফিরলেও ওই অপরাধের জন্য যাতে বাংলাদেশের নিজস্ব আইনেই অপরাধীর বিচার করা যায়, সেই মর্মে বিধান রাখা হয়। একই সাথে এই আইনে অপরাধকে জামিন-অযোগ্য করা হয় এবং গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি না নিয়ে শুধু তাকে জানানোর কথা বলা হয়।
মানবাধিকার কর্মীরা দাবি করেন, এর মাধ্যমে পুলিশের হাতে বিস্তর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই সংশোধনীর বিরোধীতা করে বাংলাদেশের তৎকালীন বিরোধীদলীয় এমপিরা সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। তারা অভিযোগ তোলে যে, দেশের নীরিহ সাধারণ মানুষকে এই আইনের ফলে ভুগতে হবে এবং তাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে।

ছবির উৎস, Getty Images
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন
বাংলাদেশে কয়েক বছর যাবত যে আইনটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে সেটির নাম - ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন।
কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে কোন অপরাধ সংগঠিত হলে সেটির প্রতিকারের জন্য ২০০৬ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন করা হয়েছিল।
পরবর্তীতে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়তে থাকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের সাথে সাথে এর মাধ্যমেও নানা অপরাধ সংগঠিত হতে থাকে।
এমন প্রেক্ষাপটে ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন প্রণয়ণ করে। তখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের বেশ কয়েকটি ধারা বিলুপ্ত করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় এসেছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন।
সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা অভিযোগ তোলেন যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের আরো কঠোর রূপটিই হলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন।
এই আইনের মাধ্যমে দেশে সরকার বিরোধীদের দমন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত করা হয় বলেও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ তুলেছে।
আইন বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক বলেন, “ওইটার ৫৭ ধারায় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ, মানহানি, কটাক্ষ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি- এইসব অপরাধের ধরণ একসাথে বলে দিয়েছিল। এইটা বাতিল করে প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য আলাদা আলাদা করে ধারা করেছে।”
তিনি বলেন, অপরাধের এসব ধরণের কার কত ক্ষতি হয়েছে সেটি পরিমাপের কোন সূত্র নেই। এমন অপরাধ যখন ফৌজদারী আইনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় তখন সেটি অপব্যবহার হতে বাধ্য।
তাদের উদ্বেগের মূল বিষয় হচ্ছে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা, গুজব রটানো বা সরকারের সমালোচনা করা- এমন সব অভিযোগে মামলা হলেই আটক করে রাখা হয় এবং আইনের অপপ্রয়োগ করা হয়।
আইনটি বাতিলের জন্য সম্পাদক, সাংবাদিক, অধিকার কর্মী ও অনেক রাজনৈতিক দল দাবি করলেও সরকার বরাবরই এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।